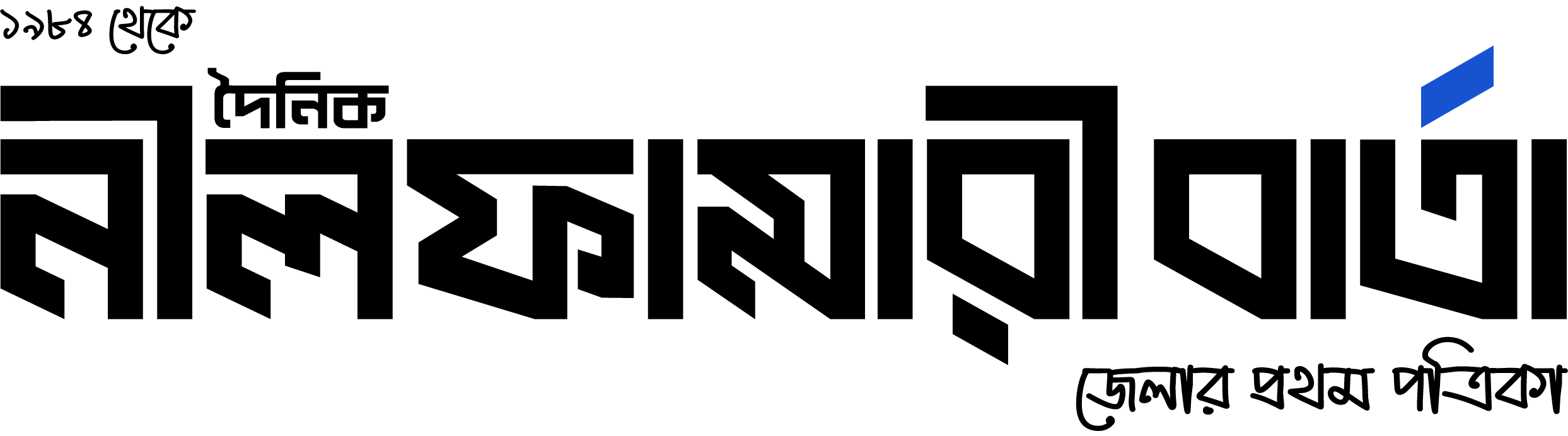মো. আবুসালেহ সেকেন্দার
ছেঁড়া দ্বীপ থেকে বাংলাবান্ধা, পদ্মা-আঁড়িয়াল খাঁর তীর থেকে সুরমা-কুশিয়ার তীরে বসবাসকারী সব বেকার যুবক কোটা ব্যবস্থার পক্ষে দেওয়া আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে। ওই আন্দোলনে তাদের পরিবার-পরিজন আত্মীয়-স্বজনদের সমর্থন রয়েছে। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শিক্ষকরা রাজপথে না থাকলেও তাদের অনেকেরই এই আন্দোলনে সমর্থন রয়েছে বলে আমার মনে হয়। এই দাবি আমাদের অনেকেরই।
আমরা যারা আর কখনও বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবো না, তাদের। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের, যারা বটতলা, আমতলা অথবা খোলা আকাশের নিচে উন্মুক্ত প্রান্তরে গড়ে ওঠা কোনও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রোদ-বৃষ্টি-ঝড় উপেক্ষা করে নিয়মিত ক্লাস পরীক্ষাতে অংশ নিচ্ছে তাদেরও। তারা আজ স্বপ্ন দেখছে, বড় হয়ে জজ-ম্যাজিস্ট্রেট হবে। কিন্তু সরকারি চাকরিতে মেধার চেয়ে কোটার পরিমাণ বেশি হলে এসব কোমলমতি শিশুদের একদিন স্বপ্নভঙ্গ হবে। তারা জীবন নিয়ে হতাশ হবে।
বিশ্বের অনেক দেশেই অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে এগিয়ে নিতে সরকারি চাকরিসহ নানান ক্ষেত্রে সীমিত পরিসরে কোটা ব্যবস্থা রাখা হয়। কিন্তু ঢালাওভাবে কোটা ব্যবস্থার প্রচলন অথবা মেধার চেয়ে কোটার ভাগ বেশি হওয়ার নজির কোথাও নেই। ওই নজির একসময় কেবল বাংলাদেশেই ছিল। তবে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের ফলে সরকার নির্বাহী আদেশে ওই কোটা ব্যবস্থা বাতিল করতে বাধ্য হয়। সরকারের ওই বাতিলের সিদ্ধান্ত আইনসম্মত ছিল না বলেই আজ আদালতে ওই বাতিলের সিদ্ধান্ত টিকছে না। সরকার যদি ওই সময় শিক্ষার্থীদের দাবি মেনে দশ ভাগ কোটা রেখে কোটা ব্যবস্থা বিলুপ্ত না করে সংস্কার করতো, তাহলে বর্তমান পরিস্থিতি সৃষ্টি হতো না।
পাকিস্তান আমলে সরকারি চাকরিতে বৈষম্য ছিল। মেধাবী হওয়া সত্ত্বেও বাঙালিদের ওই সময় সরকারি চাকরির উচ্চপদে নিয়োগ করা হতো না। সরকারি চাকরিতে বৈষম্যের বিষয়টি পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে বাঙালির দুর্বার আন্দোলনে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর সমর্থনের অন্যতম কারণও ছিল। ড. মো. মাহবুবর রহমানের মতে, ‘কেবল সিভিল সার্ভিসেই নয়, ফরেন সার্ভিস, বিভিন্ন স্বায়ত্তশাসিত ও আধা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের চাকরিতেও পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্য বিরাজমান ছিল।’ (বাংলাদেশের ইতিহাস : ১৯৪৭-৭১, পৃ. ৩৪১)।
গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, অর্থনৈতিক মুক্তি তথা বিরাজমান সরকারি চাকরিসহ সব ক্ষেত্রে বৈষম্য থেকে মুক্তিলাভ করতেই বাঙালিরা মুক্তি-সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। প্রকৃতপক্ষে যোগ্যতা-মেধার ভিত্তিতে সবার জন্যই সরকারি চাকরির দ্বার উন্মুক্ত করাও মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু স্বাধীনতার ৪২ বছর পরও কোটা পদ্ধতির নাগপাশে ওই স্বপ্ন অধরাই থেকে যায়। ২০১৬ সালে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের ফলে ওই বৈষম্যের অবসান হলেও আইনগত ত্রুটি থেকে যায়। ফলে সরকারি চাকরিতে কোটা ব্যবস্থা পুনর্বহাল করার এক রিটের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত কোটা ব্যবস্থা বহালের পক্ষে রায় দিয়েছেন। অবশ্যই আদালতের যে সংক্ষিপ্ত রায় গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে সেখানে কত ভাগ কোটা রাখা যাবে তা বলা হয়নি। অথবা ২০১৬ সালে সরকারের নির্বাহী আদেশে কোটা ব্যবস্থা বাতিল করার পূর্বের অবস্থায় ফিরে যেতে হবে কিনা সেই বিষয়ে কোনও নির্দেশনা গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়নি। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীরা কোটা ব্যবস্থা পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাওয়ার আশঙ্কা করছে। আর ওই আশঙ্কা থেকেই তারা এই আন্দোলনে জড়িয়েছে।
গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্ট মতে, সরকারবিরোধী ছাত্র সংগঠনগুলো, বিশেষ করে বাংলাদেশের বিষফোড়া জামায়াত-শিবিরের সদস্যরা এই আন্দোলন পরিচালনার পিছনে রয়েছে। বিএনপি ও তার ছাত্র সংগঠন ছাত্রদলের নামও এসেছে। কিন্তু সরকারের এই আন্দোলনকে সরকারবিরোধী আন্দোলন হিসেবে বিবেচনা করা ঠিক হবে না। বরং যৌক্তিক ও গণমানুষের দাবি, আপামর ছাত্র সমাজের দাবি মনে করে বল প্রয়োগ করে এই আন্দোলন দমন করা থেকে বিরত থাকা যথার্থ হবে বলে মনে করি। এক্ষেত্রে গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে একমত যে সরকারদলীয় ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের এই আন্দোলন দমনে বল প্রয়োগ করা হিতে বিপরীত হতে পারে। ওই ধরনের বল প্রয়োগের ফল কি হয় তা আমরা ২০১৬ সালে দেখেছি। বরং ছাত্রলীগের ঐতিহ্য ও ইতিহাস অনুসরণ করে তারা ছাত্র সমাজের এই যৌক্তিক আন্দোলনে সমর্থন দিতে পারে। সরকারের সঙ্গে ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দের সুসম্পর্ক থাকায় তারা বর্তমান সংকট সমাধানে সরকার ও ছাত্রসমাজের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করতে পারে। তারা বার্গেইনিং এজেন্ট হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারে।
চলমান সরকারি চাকরিতে কোটা বাতিলের আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে অনেকের রাজনৈতিক পরিচয় ঘাঁটলে দেখা যাবে যে তারা স্বাধীনতাবিরোধী রাজনৈতিক দল জামায়াত-শিবিরের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী মাহাতাব লিমনের মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবারকে অবমাননা ও কটূক্তি করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লেখালেখি করা থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু সব শিক্ষার্থীই মাহাতাব লিমনের মতো মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে বিষয়টি এমন নয়। বরং আমার জানা মতে, ছাত্রলীগের রাজনীতি করে, আওয়ামী লীগকে ভালোবাসে এমন অনেক শিক্ষার্থীই কোটা ব্যবস্থা পুনর্বহাল বাতিলের দাবিতে চলমান আন্দোলনে অংশগ্রহণ করছে। সুতরাং আন্দোলনকারীদের সবাইকে এক দাঁড়িপাল্লায় মাপা ঠিক হবে না। এক দাঁড়িপাল্লায় মাপলে জনপরিসরের মূল চেতনা বোঝা যাবে না। সংকট সমাধানের পথ রুদ্ধ হবে।
মনে রাখা দরকার, স্বাধীনতার পর বছরের পর বছর সাধারণ মানুষ কোটা পদ্ধতির নাগপাশে বন্দি থাকলেও মুখ ফুটে উচ্চারণ করেনি যে কোটা পদ্ধতি বাতিল করতে হবে। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষার্থী মাহতাব লিমনের মতো কতিপয় স্বাধীনতাবিরোধী চেতনার শিক্ষার্থীরা মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের অবমাননা করলেও সাধারণ শিক্ষার্থীরা কখনোই জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানহানি করেনি। ২০১৬ সালে সংঘটিত হওয়া কোটা আন্দোলনের সময়ে মুক্তিযোদ্ধাদের মর্যাদা ও সম্মান রক্ষায় তারা সচেষ্ট ছিল। তাই কোটার চেয়ে সরকারি চাকরির নিয়োগে মেধাবীদের প্রাধান্য রেখে তরুণ প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি এই ভালোবাসা ও মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি সম্মানবোধের মূল্যায়ন করা উচিত।
ঢালাওভাবে কোটার ব্যবস্থা না রেখে অসচ্ছল ও পিছিয়ে পড়া প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের উত্তরাধিকারীদের জন্য কোটার ব্যবস্থা করা হলে কেউ আপত্তি করবে বলে মনে হয় না। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন কথাই বলছে, জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানরা সুখে-শান্তিতে জীবনযাপনের বদলে কষ্টই তাদের নিত্যসঙ্গী। প্রকৃত অনেক মুক্তিযোদ্ধা আছেন, যাদের অনেকেরই মুক্তিযুদ্ধের সনদপত্র নেই। তারা সনদপত্র গ্রহণে আগ্রহবোধ করেননি। এমন বহু উদাহরণ খোঁজ নিলে পাওয়া যাবে। তাই প্রকৃতপক্ষে কোটা ব্যবস্থার মাধ্যমে অনেক মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সন্তানরা কমই উপকৃত হয়েছেন। অনেক সময়ই বিতর্ক হয়, ‘ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা’ সার্টিফিকেট নিয়ে রাষ্ট্রের অনেক সুযোগ-সুবিধা নিয়ে ফেলে। তারাও যে এই সুবিধা নিচ্ছে না- সেটা কীভাবে যাচাই করা যাবে? খুলনা জেলার ফুলতলা উপজেলায় আমার পরিচিত এমন একজন ‘ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা’ আছেন যার, বয়স মুক্তিযুদ্ধের সময় দশ বছরেরও কম ছিল। তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি তা সবাই জানে। কিন্তু তিনি টাকার বিনিময়ে কোনও না কোনোভাবে ম্যানেজ করে সনদপত্র সংগ্রহ করেছেন। তার ওই সনদপত্র সংগ্রহের ফলে তিনি ও তার পরিবার লাভবান হয়েছে। এক ছেলে কোটায় ডাক্তারি পড়েছে। অন্য ছেলে কোটায় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষ ফল না করেও বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হয়েছেন। আমার নিজ এলাকা হওয়ায় আমরা তার প্রত্যক্ষ সাক্ষী। এলাকার সবাই বিষয়টি জানলেও কিছু করার নেই। কারণ ওই ভুয়া মুক্তিযোদ্ধার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব তার সনদপত্র টিকিয়ে রেখেছে। প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধারা অভিযোগ দিলেও তার সনদপত্র অজ্ঞাত কারণে বাতিল হয়নি। এখন নাতি-নাতনি কোটায় ওই ভুয়া মুক্তিযোদ্ধার পরবর্তী প্রজন্মও সুযোগ-সুবিধা যদি পায় তা কীভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণ হবে সরকারের কাছে সেই প্রশ্ন রাখছি।
সরকারের কাছে যদি বিতর্কমুক্ত সত্যিকার মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা থাকতো তাহলেই কেবল মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের জন্য বরাদ্দ রাখা কোটা ব্যবস্থা মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য উপকারী হতো। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, কোটা ব্যবস্থায় অনেক মুক্তিযোদ্ধা ও তার পরিবারের সদস্যরা নয়, ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা ও তার পরিবারের সদস্যরা বেশি লাভবান হবে।
অন্যদিকে নারী কোটার আজ কোনও দরকার নেই। কারণ নারীরা আজ পুরুষের চেয়ে নানাদিকে এগিয়ে। মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল, ইঞ্জিনিয়ারিংসহ নানা পরীক্ষায় তারা ছেলেদের টপকিয়ে শীর্ষস্থান অধিকার করছেন। বিসিএস পরীক্ষায় প্রথম হওয়ার কৃতিত্বও তাদের রয়েছে। তাই অনগ্রসর শ্রেণি হিসেবে বিবেচনা করে তাদের জন্য বিশেষ কোটার যৌক্তিকতা এখন আর নেই। আর নারীদের জন্য কোটা পদ্ধতির বিরোধিতা অনেক নারী শিক্ষার্থী করছেন। কারণ কোটা পদ্ধতি রেখে প্রকৃতপক্ষে তারা যে পুরুষের তুলনায় কম যোগ্য সে বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে; যা তাদের জন্য মর্যাদাহানিকরও বটে।
বর্তমানে জেলা বা বিভাগীয় কোটার কোনও প্রয়োজন নেই। কারণ এখন জেলা শহর আর ঢাকা শহরের মধ্যে খুব বেশি সুযোগ-সুবিধার পার্থক্য নেই। জেলায় জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে মানসম্মত শিক্ষা শিক্ষার্থীরা জেলায় বসেই অর্জন করতে পারবে। একসময় উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোকে অনগ্রসর বলা হতো। কিন্তু রংপুর-বগুড়াসহ উত্তরাঞ্চলের অনেক জেলায় বর্তমান সরকারের আমলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হওয়ায় সেই চিত্র পাল্টে গেছে। এজন্য অবশ্যই বর্তমান সরকার সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রেখেছে। নারী শিক্ষার বিস্তার এবং গ্রামে গ্রামে উন্নয়ন তারাই সফলভাবে করে যাচ্ছে।
তবে কোটা ব্যবস্থা একেবারে বিলুপ্তি না করে উত্তর আধুনিক বাংলাদেশে কোটা পদ্ধতির যৌক্তিকতা নিয়ে পুনর্মূল্যায়ন করা যেতে পারে। ২০১৫ সালের পূর্বে মেধার চেয়ে কোটায় বেশি নিয়োগের পদ্ধতিতে ফিরে না গিয়ে সীমিত পরিসরে কোটা ব্যবস্থা পুনর্বহাল করে বর্তমান সংকটের সমাধান করা যেতে পারে।
মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে কেবল অনগ্রসর প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবারের জন্য সরকারি চাকরিতে পাঁচ ভাগ কোটার ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে। উপজাতি, প্রতিবন্ধী, হিজড়াসহ অন্য পিছয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর বাকি পাঁচ ভাগ কোটা ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে। সরকারি চাকরিতে দশভাগ কোটাই যৌক্তিক। বর্তমান সময়ের সামগ্রিক দিক বিবেচনায় এর চেয়ে বেশি কোটা না রাখলেই মনে হয় এখন ভালো।
আর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারসহ অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে এগিয়ে নিতে ভিন্নভাবে সহযোগিতা করা যেতে পারে। তারা যাতে মেধাবীদের সঙ্গে সমান প্রতিযোগিতা করে সরকারি চাকরিতে উত্তীর্ণ হতে পারেন সেভাবে তাদের গড়ে তুলতে নানা উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে।
মুক্তিযোদ্ধাদের ও তাদের পরিবারের সচ্ছলতার জন্য তাদের ভাতা বৃদ্ধিসহ নানা ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ, হিজড়া ও উপজাতিদের যোগ্য করে গড়ে তুললে তাদের জন্য অধিক সংখ্যক বৃত্তি প্রদানে সরকার উদ্যোগী হতে পারে। কিন্তু কোটার নামে অযোগ্য, অদক্ষ, কম মেধাবীদের সরকারি চাকরিতে অধিক সুযোগ বৃদ্ধি কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।
লেখক: সহকারী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।